আজকের আলোচনার বিষয়ঃ “ভারতীয় অর্থনীতির” উত্থান ও পতন। এটি জনাব আকবর আলি খান এর বহুল-পঠিত একটি প্রবন্ধ। আকবর আলি খান (১৯৪৪ – ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২) ছিলেন একজন বাংলাদেশি সরকারি আমলা, অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি হবিগঞ্জের মহুকুমা প্রশাসক বা এসডিও ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন সক্রিয়ভাবে মুজিবনগর সরকারের সাথে কাজ করেন।
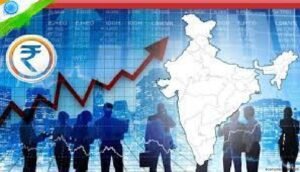
“ভারতীয় অর্থনীতির” উত্থান ও পতন
একবার জনৈক পাদ্রীকে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে ফারাক ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। পাদ্রী বললেন, “স্বর্গ ও নরকের মধ্যে তফাৎ অতি নগণ্য, সামান্য পরিবর্তন হলেই বেহেশত দোজখে পরিণত হয়। ” তাজ্জব হয়ে শ্রোতারা পাদ্রীকে উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানায়। পাদ্রী বললেন, “ধরুন স্বর্গ হচ্ছে এমন এক দেশ যেখানে পুলিশ হল ইংরেজ, বাবুর্চিরা বাঙ্গালী, চিত্রকররা ফরাসী আর জার্মানরা হল প্রকৌশলী। নরক হচ্ছে সে দেশ, যে দেশে বাঙ্গালীরা পুলিশ, ইংরেজরা পাচক, চিত্রকররা জার্মান আর ফরাসীরা প্রকৌশলী।”
স্বর্গ ও নরকের ফারাক সম্পর্কে পাদ্রী সায়েবের বক্তব্যের সাথে অনেকেই একমত হবেন না। তবে বিভিন্ন জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি যা বলেছেন, অধিকাংশ লোকই তা অকপটে মেনে নেবে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একটি বহুল প্রচারিত ধারণা হল, প্রতিটি মানুষের যেমন ভিন্ন চরিত্র থাকে তেমনি প্রতিটি জাতিরই রয়েছে সুস্পষ্ট চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য। রোমান্টিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা হেগেল ও হার্ডার-এর মতে প্রতিটি জাতির একটি জৈব সত্তা রয়েছে। এই সত্তাই হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চালিকা শক্তি।
রাজনৈতিক দর্শনের মত অর্থনীতির সূত্রপাত হয় জাতিকে সমৃদ্ধতর করার স্বপ্ন নিয়ে। অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ অর্থনীতি বিষয়ক তাঁর প্রথম গ্রন্থের তাই নাম রাখেন “An Enquiry into Causes and Wealth of Nations” (জাতিসমূহের সম্পদ এবং এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান)। জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোই হচ্ছে ধ্রুপদী অর্থনীতির উপজীব্য বিষয়। পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদ্রা ভোক্তা ও উৎপাদকদের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন। তবু অর্থনীতির পরিধি শুধু ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। সমষ্টিগত অর্থনীতি বিশ্লেষণ করতে হলে এখনও রাষ্ট্রই (যা প্রধানত জাতিভিত্তিক) হচ্ছে মূল একক।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রেরই লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের কল্যাণ। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাথে অর্থনীতিবিদদের একটি বড় তফাৎ রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক অঙ্গনের কুশীলবদের আচরণ একই ধরনের নয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের একটি মৌলিক প্রতীতি হল যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলেরই (রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি যাই হোক না কেন) আচরণই অভিন্ন। জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক আচরণে আদৌ প্রতিফলিত হয় না। অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাই ভারতের জন্য স্বতন্ত্র “ভারতীয় অর্থনীতি” অথবা বিলাতের জন্য “ব্রিটিশ অর্থনীতির” প্রয়োজন নেই।

এ কথা অনুমান করা মোটেও সঠিক হবে না যে, অর্থনীতিবিদগণ জাতির ও রাষ্ট্রের বিভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞ; আর তাই তারা বিশ্বাস করেন যে, সকল জাতি একই ধরনের ব্যবহার করে । বরং তার উল্টোটিই সত্য। আঠার ও উনিশ শতকে মূলধারার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই ছিলেন ইংরেজ। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। উনিশ শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেল তাঁর Philosophy of History গ্রন্থে লিখেছেন:
India has always been the land of imaginative inspiration, and appears to us still as a fairy region, an enchanted world. (ভারত আমাদের কাছে সব সময়েই ছিল কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপনার দেশ এবং এখনও আমাদের কাছে মনে হয় রূপকথার দেশ – একটি মায়াবী জগত।)
মূলধারার অনেক ইংরেজ অর্থনীতিবিদের জ্ঞান শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এঁদের অনেকেই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে ভারতকে নিবিড়ভাবে জানতেন । ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ স্যার জেমস স্টুয়ার্ট বাংলার মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে পরামর্শ দিয়েছেন। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন সক্রিয় শেয়ার মালিক ছিলেন।
প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথুস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হাইলিবারি কলেজে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের অর্থনীতি পড়িয়েছেন। হিতবাদের (utilitarianism) প্রবক্তা স্যার জেমস মিল ও স্যার জন স্টুয়ার্ট মিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক পদে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ কেইনস ইন্ডিয়া অফিসে শিক্ষানবিস হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।
ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন রবার্ট টরেনস (Robert Torrens), জন র্যামজে ম্যাককুলক (John Ramsay Mcculloch), স্ট্যানলি জেডনস (Stanley Jevons) ও আলফ্রেড মার্শাল। ফরাসী অর্থনীতিবিদ জঁ ব্যাপটিস্ট সে (Jean Baptiste Say) এবং কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে লিখেছেন । কিন্তু এঁদের কেউই কখনও স্বীকার করেননি যে, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অথবা ভিন্ন ধরনের জাতীয় চরিত্রের ফলে দক্ষিণ এশিয়াতে শিল্পোন্নত অর্থনীতির সূত্রসমূহ প্রযোজ্য নয়। প্লেটোর সময় হতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জাতীয় চরিত্রের ভিন্নতার তাৎপর্য স্বীকার করেন, অথচ মূলধারার অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য একেবারেই উপেক্ষিত।
মূলধারার ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে উনিশ শতকে তিন ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়।
প্রথমত, জার্মানিতে ঐতিহাসিক ঘরানার (Historical School) |নীতিবিদগণ বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সূত্র অস্বীকার করেন।
দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে | প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) অর্থনীতিবিদগণ মূলধারার অনেক অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন ।
তৃতীয়ত, মার্কসবাদ মূলধারার অর্থনৈতিক সূত্রসমূহের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। তবে মূলধারার অর্থনীতির বিরুদ্ধে উনিশ শতকে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ দেখা দেয় ভারতে। এ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন রাজনীতিবিদগণ, অর্থনীতিবিদগণ নয়। এর কারণ হল উনিশ শতকে ভারতে অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখার মর্যাদা লাভ করেনি। ভারতে অর্থনীতি বিভাগ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই ঊনিশ শতকে ভারতে কোন পেশাদার অর্থনীতিবিদ ছিল না; প্রধানত রাজনীতিবিদগণই অর্থনীতির চর্চা করতেন।

ধ্রুপদী অর্থনীতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী বক্তব্য হল ভারতীয় রাজনীতিবিদগণের সম্পদ পাচার তত্ত্ব (drain theory)। ধ্রুপদী অর্থনীতির আগে বণিকবাসী ( mercantilist) ঘরানার অর্থনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে হার-জিতের খেলা (zero-sum game) হিসাবে গণ্য করতেন। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যারা বেচে তারা লাভ করে; যারা কেনে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কিন্তু ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো তাঁর তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) তত্ত্বে প্রমাণ করেন যে, বাণিজ্যের ফলে যারা কেনে আর যারা বেচে উভয়েই লাভবান হয়।
বাণিজ্য হার-জিতের খেলা নয়, বাণিজ্য উভয় পক্ষের জিতের খেলা (win-win pame)। পক্ষান্তরে ভারতীয় রাজনীতিবিদ দাদাভাই নৌরজী (১৮২৫-১৯১৭) বাণিজ্যের সুফল সম্পর্কে ধ্রুপদী মতবাদ চ্যালেঞ্জ করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাণিজ্য হচ্ছে। ভারতের মত অনুন্নত দেশ হতে উন্নত দেশে সম্পদ পাচারের হাতিয়ার মাত্র। পরবর্তী কালে এই বক্তব্য বিকশিত হয় প্রশাসক-পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের হাতে। দাদাভাই নীরজীর বক্তব্য প্রথমে ১৮৬৭ হতে ১৮৭০ সনের মধ্যে কয়েকটি নিবন্ধে প্রকাশিত ১৯০০ সালে এসব প্রবন্ধ নৌরজীর “Poverty and the Un British Rule in [ India” নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়।
দাদাভাই নৌরজীর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, উনিশ শতকে অংশীদারদের তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে ভারতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠেনি; গড়ে উঠেছে ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পদ পাচারের হাতিয়ার হিসাবে। ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর খরচ, ভারতে ব্রিটিশ বেসামরিক প্রশাসকদের বেতন ও পেনশন এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল বাবদ ভারত থেকে প্রতি বছর হলুদ পাঠাতে হয়েছে।
সম্পদ পাচার তত্ত্বের প্রবক্তাদের হিসাবে প্রতি বছরে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদের ১.২ শতাংশ হতে ১.৫ শতাংশ সম্পদ পাচার হয়ে যেত। প্রখ্যাত | অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্তের সিদ্ধান্ত হল “প্রতি বছরে পাচারকৃত সম্পদ হল ভারতের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতি, দেশ থেকে যে অর্থ বেরিয়ে যায় তা আর কোন রূপেই ফিরে আসে। না; একটি গরীব দেশের সম্পদ ধনী দেশের শিল্প বাণিজ্যকে ফলবান করে তুলছে।”
জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে ভারত থেকে সম্পদ পাচার হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের নগ্নতম বহিঃপ্রকাশ। ভারতের জনগণ তাই সম্পদ পাচারকে অকাট্য সত্য রূপে গ্রহণ করে। এই তত্ত্বের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দুটো অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে, একটি হল তাত্ত্বিক, অন্যটি হল প্রায়োগিক।
তাত্ত্বিক বিচারে, ভারতে বহির্বাণিজ্যের কুফল সম্পর্কে শুধু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণই প্রশ্ন তুলেননি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত অনল-বর্ষী জাতীয়তাবাদীগণও সংশয় প্রকাশ করেছেন। “বঙ্গ দেশের কৃষক” নিবন্ধে উনিশ শতকের শেষ দিকে বঙ্কিম লেখেন, “এ সকল তত্ত্ব যাহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে।
যে বিপুল রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্ধ কাহার?” বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি দেখা যায় ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এল. সি. এ. নোলস (L. C A Knowles)-এর লেখাতে। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে উদ্বৃত্ত থাকত তার একতৃতীয়াংশ ভারতে প্রধানত রেলওয়েতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের সুদ হিসাবে গিয়েছে, আর একতৃতীয়াংশ দিয়ে ভারত বাইরে থেকে সোনা-রূপা আমদানী করেছে। সর্বাধিক একতৃতীয়াংশ ব্রিটিশ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হয়েছে।
এ ব্যয়ের ফলে তাঁর মতে ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পাঁচ দশক পরে আজ দাদাভাই নৌরজী অথবা রমেশচন্দ্র দত্ত নয়, বরং বঙ্কিমচন্দ্র ও নোলস সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন। দাদাভাই নৌরজী ও জাতীয়তাবাদী লেখকগণ ভারতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের সুদ আসল পরিশোধকে সম্পদ পাচার হিসাবে গণ্য করতেন । আজকে একই শর্তে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ভারত সরকার হন্যে হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে।
জাতীয়তাবাদী নেতারা এক সময়ে বিদেশী প্রশাসকদের বেতনকে সম্পদের পাচার বিবেচনা করতেন । অথচ আজকের ভারতে বিদেশী পরামর্শক ও বহুজাতিক কোম্পানীর কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক মুদ্রায় বেতন দিতে কোন কুণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না।
প্রায়োগিক দিক থেকে বড় প্রশ্ন হল, ভারত হতে পাচারকৃত সম্পদের প্রকৃত গুরুত্ব কতটুকু। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে প্রতি বছর পাচারকৃত সম্পদের পরিমাণ মোট বার্ষিক জাতীয় উৎপাদের দু’শ ভাগের এক ভাগ (৫%) হতে পারে। জাতীয়তাবাদীদের হিসাবে এ পরিমাণ আড়াই হতে তিন গুণ বেশি। জাতীয়তাবাদী নেতাদের হিসাব অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

সম্পদ পাচার তত্ত্বের দুর্বলতা সত্ত্বেও এর অপরিসীম ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সম্পদ পাচার তত্ত্ব হল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে পুরান অথচ পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব। এটি অত্যন্ত ভুল ধারণা যে, কার্ল মার্কস সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বের জনক। মার্কস সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন তত্ত্বই লেখেননি। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখক হবসন (Hobson) তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯০২ সালে। উপরন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম তত্ত্ব প্রণয়ন করেন রোজা লুক্সমবার্গ ও লেনিন। রোজা লুক্সেমবার্গের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে আর লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।
ভারতীয় অর্থনীতি শুধু ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতীয় অর্থনীতির প্রবক্তাগণ অর্থনীতির একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করান। এঁদের মতে “ভারতীয় অর্থনীতি” একটি ফলিত শাস্ত্র নয়, এটি একটি মৌলিক শাস্ত্র। পশ্চিমা অর্থনৈতিক সূত্র প্রয়োগ করে “ভারতীয় অর্থনীতির” চর্চা সম্ভব নয়। “ভারতীয় অর্থনীতির” প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, অর্থনীতির কোন বিশ্বজনীন সূত্র নেই, দেশ কাল পাত্র ভেদে এর তফাৎ ঘটবে।
অর্থনীতি যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় না। এর পেছনে থাকে একটি সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত কাঠামো। ভারতীয় অর্থনীতির উপজীব্য বিষয় হল তাই ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক স্বকীয়তা – যা তার অর্থ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। “ভারতীয় অর্থনীতি” অভিব্যক্তির প্রথম প্রচলন করেন প্রখ্যাত বিচারক, সমাজ সংস্কারক ও ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে (১৮৪২-১৯০১)।
তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখার্জি, ভি, জি, কালে প্রমুখ। যদিও ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের মিল রয়েছে, তবু প্রকরণগত দিক হতে এঁদের দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : ঐতিহাসিক ঘরানা ও রোমন্টিক ঘরানা।
ঐতিহাসিক ঘরানার ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ জার্মান ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই ঘরানার পথিকৃৎ ছিলেন রানাডে নিজে। * রানাডের দুটো মূল বক্তব্য ছিল। প্রথমত, রানাডে ছিলেন সমাজসংস্কারক। তিনি মনে করতেন, ধর্মের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর মতে ধর্মীয় কুসংস্কার হল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।
তাই তিনি মনে করতেন যে, ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে খৃষ্টানদের প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের মত সংস্কারবাদী আন্দোলনের আলোকে হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করতে নিশ্চিত করবে না। জার্মান ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদদের অনুকরণে তিনি হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে বাজারের অদৃশ্য হাত নিজে নিজে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
জার্মান ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদদের মতই রানাডে ছিলেন রক্ষণশীল সংস্কারক। ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদদের মত তিনি একটি বিভক্ত, দুর্বল ও প্রধানত কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে একটি গতিশীল শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের উদ্যোগ সমর্থন করেন। সাথে সাথে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সমর্থন করেন।
রানাডের মত ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদগণ শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের পক্ষে ছিলেন। তবে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়ন নিজে নিজে হবে না, ভারতকে তার নিজের পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক রূপান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। রোমান্টিক ধারার ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের বক্তব্য হল যে, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়ন ভারতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য বাইরের পরিবর্তন আত্মস্থ করা নয়, বরং বাইরের আঘাত সত্ত্বেও ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তাকে রক্ষা করা।
এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর মতে পার্থিব ভোগবিলাস জীবনকে সমৃদ্ধতর করে না, বরং জ্বালাযন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়। গান্ধীর মতে ভোগের সম্প্রসারণ নয়, সংকোচনই হল অর্থনৈতিক মুক্তির উপায়। গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদে রয়েছে মার্কিন অর্থনীতিবিদ হেনরি জর্জ ও ফরাসী প্রাকৃতিক-বিধিবাদী (physiocratic) ঘরানার অর্থনীতিবিদদের প্রভাব। এঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন যে কৃষিই হল সম্পদের একমাত্র উৎস। গান্ধীর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল, স্বনির্ভর গ্রামসমূহে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে উত্তাল তরঙ্গের জন্ম নিলেও তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন অতি মুষ্টিমেয় শিষ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাঁরা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের অনেকেরই গান্ধীর অর্থনৈতিক দর্শনে আস্থা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পার। রাজনৈতিকভাবে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক দর্শনে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে তিনি গান্ধীর অর্থনৈতিক দর্শনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি উল্লেখ করেন। প্রথমত, শরত্তন্দ্র ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিকে গান্ধীর মত অবনতির লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করতেন না। তাই তিনি লিখেছেন:
“একটা কথা পুরানোপন্থীদের মুখে দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না, এখন চাষারা পর্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। প্রত্যুত্তরে তাদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয় ত আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্নে না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে; তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা – তাকে স্বীকার করে তার গোলামি করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।
দ্বিতীয়ত, গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, কুটির শিল্প আধুনিক শিল্পের চেয়ে শ্রেয়। শরৎচন্দ্র এ যুক্তি মানেননি। তাই তিনি বলেন, “কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।” বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই ধরনের মত পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন
The programme of the charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.
(চরকা কর্মসূচী এতই বালসুলভ যে এ কর্মসূচী সারাদেশকে যেভাবে বিভ্রান্ত করছে তাতে যে কেউ নিরাশ হয়ে পড়বে।)
প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর স্বপ্ন আর ভারতের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলে। গত একশ বছর ধরে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভাবিত উন্নতির ফলে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেছে। এ জনসংখ্যার চাহিদা সনাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মিটানো সম্ভব ছিল না। গান্ধীর স্বপ্নের গ্রামগুলি ছিল সম্প্রীতির আর শাস্তির নীড়। বাস্তবে ভারতীয় গ্রাম হল গোপন হিংসায় বিদীর্ণ এক সমাজ- যেখানে জীবন, দার্শনিক হবসের ভাষায়, “দরিদ্র, নোংরা, পাশবিক ও হ্রস্ব।” গান্ধীজীর শিষ্যরাই গান্ধীজীকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়েছে।
ভারত-ভাগ্য বিধাতারা মুখে মুখে গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে একটি আধুনিক ও শিল্পায়িত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথে চলেনি, চলেছে রানাডের মত ঐতিহাসিক ঘরানার অর্থনীতিবিদদের নীল-নকশা অনুসারে। উপরন্তু কার্ল মার্কসের ভাবধারাও জওহরলালের মত গান্ধীর ভাবশিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেছে।
১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রেক্ষিতে “ভারতীয় অর্থনীতির মূল বক্তব্যসমূহ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। নব্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার এগিয়ে আসে। তবে রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে “ভারতীয় অর্থনীতি” চর্চায় নবজাগরণ দেখা দেয়নি, বরং ভাটা দেখা দেয়। এর কারণ হল কাছাকাছি সময়ে অন্য যে সব এশীয় ও আফ্রিকান দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাও ছিল একই ধরনের।
ভারতীয় অর্থনীতির মূল সূত্রসমূহ শুধু ভারতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর-পর অর্থনীতির একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে “উন্নয়ন অর্থনীতি” আবির্ভূত হয়। গত পাঁচ দশক ধরে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতিপাদ্য বক্তব্যসমূহ উন্নয়ন অর্থনীতির মূলধারার অঙ্গীভূত হয়ে দাঁড়ায় ।
উন্নয়ন অর্থনীতির বক্তব্যসমূহ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ বক্তব্য মূলধারার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদেরও সমর্থন লাভ করে। আনুমানিক ১৯৮০ পর্যন্ত সকল উন্নয়নশীল দেশেই এই নতুন শাস্ত্রের সুপারিশসমূহ ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। উন্নয়ন অর্থনীতির মূল সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ।
প্রথমত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে একটা বি ধাক্কার (big push) সৃষ্টি করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন অর্থনীতির দ্বৈত সত্তা রয়েছে একধারে রয়েছে চিরাচরিত খাত, অন্যদিকে আধুনিক খাত।
কাজেই আধুনিক অর্থনীতির সকল সুপারিশ উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
তৃতীয়ত, বাজারের অদৃশ্য হাত উন্নয়নশীল দেশে সক্রিয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাজার নেই, অনেক ক্ষেত্রে বাজার অকার্যকর ও অসম্পূর্ণ । কাজেই সরকারকে অর্থনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হয়।
চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশকে শোষণের একটা প্রক্রিয়া।
তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি দেশকে আমদানী-বিকল্প নীতি অনুসরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করবে এবং নিজেদের পণ্যের বাজার সৃষ্টি করবে। কাজেই শিশু শিল্পের সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে হবে ।

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সূত্র হতে প্রচুর সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উন্নয়ন অর্থনীতির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র অটুট থেকে যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষে দশকের পর দশক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিম্ন হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এ ধরনের ৪ হতে ৫ শতাংশের প্রবৃদ্ধিকে অর্থনীতিবিদগণ ঠাট্টা করে “হিন্দু প্রবৃদ্ধির হার” নাম দিয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ উন্নয়ন অর্থনীতির মৌল সুপারিশের ব্যতিক্রম করে বাজার বৎসল ও রপ্তানী-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
দেখা গেল যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। বস্তুত উন্নয়ন অর্থনীতির সুপারিশ অনুসরণ করে আদৌ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যাবে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে বিগত দশকের একটি গল্প মনে পড়ছে। কথিত আছে যে একজন ইহুদি, একজন রাশিয়ান ও একজন ভারতীয় দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে বর চাইতে যান। ইহুদি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দ্র বললেন যে তিনি এ ব্যাপারে অনেক কাজ করেছেন; তাই আগামী দশ হতে পনের বছরে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।
রাশিয়ার লোকটি ইন্দ্রের কাছে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভিক্ষা করেন। ইন্দ্র জবাবে বলেন যে, কাজটি কঠিন, তবে হয়ত আগামী বিশ-পঁচিশ বছরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার ভারতীয় ব্যক্তিটি দক্ষিণ এশিয়া থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের বর চান। ভারতীয় লোকটির বক্তব্য শুনে ইন্দ্ৰ কেঁদে ফেলেন এবং বলেন যে, তিনিও দক্ষিণ এশিয়া থেকে দারিদ্র দূর করতে চান, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এ কাজটি হাসিল হবে কি না সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন।
ভারতে গত দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্য নৈরাশ্যবাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করেছে। বাণিজ্য উদারকরণ, বহির্মুখী ও বাজার-বৎসল নীতি অনুসরণের ফলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ভারতের অর্থনীতির কোন অন্তর্নিহিত সমস্যা নেই। সমস্যা হল উন্নয়ন অর্থনীতির ভ্রান্ত নীতিমালা। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ক্ষুদ্র-শার্দুল অর্থনীতিসমূহের সাফল্য উন্নয়ন অর্থনীতির মৌল অনুমান সম্পর্কে দু’ধরনের তাত্ত্বিক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।
প্রথমত, উন্নয়ন অর্থনীতির একটি মূল বক্তব্য হল যে, বাজারের ব্যর্থতা হেতু উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যর্থতা বাজারের ব্যর্থতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে অনেক দেশেই আমলাতন্ত্র তস্করতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পারমিট আর লাইসেন্সের নামে অনুপার্জিত মুনাফাখোররা “লাইসেন্স-রাজ” প্রতিষ্ঠা করে অর্থনীতির সৃজনশীলতাকে পঙ্গু করেছে।
অর্থনীতিবিদ এ্যান ক্রুগার রাষ্ট্রের ত্রুটিকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন : “করার ত্রুটি” (failures of commission) এবং “না করার ত্রুটি (failures of omission)। “করার ত্রুটির” মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকসান এবং উন্নয়নের নামে সরকারের অপচয়। “না করার ত্রুটির” মধ্যে রয়েছে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকর সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতিমালা (যথা বিনিময় হারের অতিমূল্যায়ন অথবা উচ্চ হারে মূল্যস্ফীতি) অনুসরণ। সামগ্রিকভাবে সরকারের ব্যর্থতা বাজারের ব্যর্থতাকে ছাড়িয়ে গেছে।
দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন অর্থনীতির একটি বড় বক্তব্য হল যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের রীতিনীতি, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ভিন্ন ধরনের তত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ শুধু বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বাজার অর্থনীতির বাইরের বিষয়সমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও এদের প্রয়োগ সম্ভব।
এ সব বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিবেচনা করলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রথা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটেও অযৌক্তিক নয়। উন্নয়নশীল দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষারা উন্নত দেশের কৃষকদের চেয়ে কোন অংশেই কম বুদ্ধিমান বা কম যৌক্তিক নয়। উন্নয়নশীল দেশের জন্য মোটেও ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োজন নেই । দীপক লাল যথার্থই লিখেছেন,
Nor are the so-called institutional features of the third world, such as their strange social and agrarian structures or their usurious informal credit systems necessarily a handicap to growth. They are likely to represent an efficient, second best adaptation to the risks and uncertainties inevitable in the relevant economic environment In the absence of other means of eliminating or alleviating risks, the destruction of these traditional institutions could actually do more harm than good. (তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যথা তাদের অদ্ভুত সমাজের বা
কৃষির অদ্ভুত কাঠামো অথবা চড়া সুদের অনানুষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিশ্চিত অন্তরায় নয়। তারা সম্ভবত সংশ্লিষ্ট আর্থিক পরিবেশে অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কার্যকর ও সম্ভবশ্রেষ্ঠ অভিযোজন করে। ঝুঁকি দূর বা হ্রাস করা সম্ভব না হলে সনাতন প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করবে।) কাজেই মূলধারার বাইরে উন্নয়ন অর্থনীতি সংক্রান্ত স্বতন্ত্র তত্ত্বের আদৌ প্রয়োজন নেই ।
প্রকৃতপক্ষে গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিকভাবে উন্নয়ন অর্থনীতির মূল বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেছে। তাত্ত্বিকভাবেও এর মূল বক্তব্যসমূহের অসম্পূর্ণতা আজ সুস্পষ্ট । আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, উন্নয়ন অর্থনীতি এবং তার পূর্বসূরী ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে মতবাদ গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তবে পল ক্রুগম্যান ঠিকই। বলেছেন: “Economic fallacies never die at best they slowly fade away. ” (অর্থনীতির ভ্রান্ত মতবাদসমূহ কখনও মরে না – খুব বেশি হলে এরা ধীরে ধীরে লীন হয়ে যায়)।
প্রকৃতপক্ষে অনেক ভ্রান্ত অর্থনৈতিক মতবাদই বার বার ফিরে আসে। “ভারতীয় অর্থনীতি” ও “উন্নয়ন অর্থনীতি” দক্ষিণ এশিয়ার জনমনে দুটো ধারণার সৃষ্টি। করেছে যা “উন্নয়ন অর্থনীতি” তত্ত্ব হিসাবে হারিয়ে গেলেও লুপ্ত হবে না। প্রথমত, দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ বহির্বাণিজ্যকে সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখবে। বিশ্বায়নের সুফলের কথা যতই বলা হোক না কেন, দক্ষিণ এশিয়াতে সহজে উদার বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ দূরীভূত হবে না।
দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদগণের দীর্ঘদিনের প্রচারের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ বাজারের অদৃশ্য হাতের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না, বরং তারা বাজারকে অবিশ্বাস করে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ রাষ্ট্রের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। সংরক্ষণের দেওয়ালের আড়ালে শিল্পায়নের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পক্ষে দাবি দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার থাকবে। “ভারতীয় অর্থনীতি” ও তার উত্তরাধিকারী “উন্নয়ন অর্থনীতির” তত্ত্ব মরুপথে হারিয়ে গেলেও, তাদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি দীর্ঘদিন ধরে শোনা যাবে। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের তাই মূল্যায়ন হবে। “জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।”
আরও দেখুনঃ
